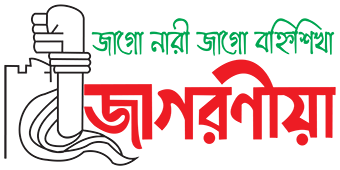উনিশ শতকে বাংলায় নারী পুরুষ সম্পর্ক (চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়)
প্রকাশ | ৩০ জুন ২০১৭, ০০:৩৬

উনিশ শতকে বাংলায় নারী পুরুষ সম্পর্ক, বিলকিস রহমান রচিত প্রথম গ্রন্থ, তার গবেষণার আলোকে লেখা। পড়ে শেষ করলাম বইটি, পড়তে যেয়ে একটু বেশি সময় নিয়েছি, নিতে হয়েছে। আমাকে ভাবিয়েছে বইটি, তথ্য উপাত্ত অবাক করেছে, কখনও কষ্ট পেয়েছি, গুমরে কান্না নিয়ে কাটিয়েছি অনেকটা সময়। নিজের অজান্তেই করুণাও হয়েছে এই সময়ের কিছু নারী জীবন দেখে। সেই বৈরী সময়ের কতোটা পাড়ি দিয়ে এসেছি আমরা যদি তা উপলব্ধি করতো তাহলে স্বেচ্ছায় কেউ কেউ যেমন জীবনধারা বেছে নিয়েছে তা ভাবাতো, নিশ্চয়ই ভাবাতো!!!
এবং বলে নিতে চাই, আমি নিতান্তই একজন সামান্য পাঠক হিসেবে এটি পড়তে যেয়ে যা আমাকে ভাবিয়েছে এবং মনে হয়েছে আরো আলোচনার দাবী রাখে সেই হিসেবেই পুরো বইটি’র একটা চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছি।
চতুর্থ অধ্যায়: বিবাহ বহির্ভূত নারীপুরুষ সম্পর্ক
লেখক শুরুতেই বলছেন সেই সময়ের সামাজিক ও ধর্মীয় নিয়মে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ছিল গর্হিত। এ সত্ত্বেও বাস্তবে তা দেখা যায় উনিশ শতকে, তারই বিষদ আলোচনা আছে এই অধ্যায়ে।
উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ইংরেজ শাসক ও ব্যবসায়ীগণ অধিকাংশ পরিবার ছাড়া এদেশে বসবাস করতেন। সামাজিক নৈতিকতা কাঠামো ভেঙে পড়ার এটি একটি প্রধান কারণ। ঔপনিবেশিক শাসকদের গৃহে দেশি নারী, বেশীর ভাগই বিধবা, নানা কারণে সমাজ থেকে উৎখাত হওয়া নারী বা ক্রীতদাসী তাদের থাকা ছিল অতি সাধারণ বৈশিষ্ট্য।
কলকাতায় বসবাসকারী দেশি বাবুদের বাড়িতেও একই চিত্র। উনিশ শতকে প্রতিটি বাজার ও জমিদার কাচারিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে দেহব্যবসা, বেশ্যালয়।
সেই সময়ের সংবাদ সাময়িকপত্র, নাটক, উপন্যাস, প্রহসন, আত্মজীবনী এবং সরকারি নথিপত্রে একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের সম্পর্কের খবর যেমন – উপপত্নী বা রক্ষিতা, দাসী-বাঁদী কিংবা বারাঙ্গনা প্রসঙ্গ। লেখক তা উঠিয়ে এনেছেন এই অধ্যায়ে।
১
লেখক জানাচ্ছেন, উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাড়িতেই স্ত্রী ও বাগানবাড়িতে উপপত্নী রাখার চর্চা চলছিল। এবং সেকালের কলকাতার নতুন ধনী ‘বাবু’দের পরিবারে স্ত্রীর ভাগ্যে স্বামীর দাসত্বটুকুও জুটতো না। এসব বাবুদের অনেকেই সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্ব হিসেবে বিয়ে করতেন এবং হয়তো স্ত্রীকে দু’একটি সন্তানও উপহার দিতেন। কিন্ত এরা অনেকেই স্ত্রীর সঙ্গে কার্যত কোনো সম্পর্ক রাখতেন না।
২
উনিশ শতকে বাংলায় পতিতাবৃত্তি সমাজের প্রান্তসীমা পার হয়ে ব্যাপক পরিসরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছিল। ব্রিটিশরাজ বিভিন্ন আইনের দ্বারা পতিতাবৃত্তি নিবারণের জন্য পতিতাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন। লেখক সেই সময়ের প্রশ্নমালাটিও এখানে তুলে ধরেছেন।
জানা যায় সেই সময় সিলেট অঞ্চলে রক্ষিতা বউদের বলা হতো ‘খাদিমা বউ’। খেদমত করার জন্য রাখা হতো এই ‘খাদিমা’ কে, আসল বউ কোনো কাজ করবে না। খাদিম তার সেবা যত্ন করবে। যদি খাদিমার ঘরে কোনো সন্তান হয় তবে সে সন্তান অবশ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে সম্পত্তি পেতো।
উনিশ শতকের বাংলায় সামাজিক চিত্রে কুলীনপ্রথা একটি বিশেষ স্থান দখল করেছিল এবং একাদশ শতকের রাজা প্রসন্ন সেনের আমলে বাংলাদেশে এই প্রথার প্রচলন হলেও উনিশ শতকে এসে ভয়াবহ রূপ নেয়।
এই প্রথার কারণে অনেক কন্যাকে আজীবন কুমারী থাকতে হতো অথবা সধবা হয়েও বাপের বাড়িতেই থাকতে হতো। অনেক সময় কারো কারো কাছে এই জীবন দুঃসহ হয়ে উঠতো এবং পুরুষের প্ররোচনায় অনেক মেয়েই সমাজের বাইরে পা রাখতে বাধ্য হতো। তখন তাদের কাছে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ ছাড়া অন্য কোনো রাস্তা খোলা থাকতো না।
বিবাহ কুলীনদের ব্যবসায় পরিণত হয়। উইলিয়াম হান্টারের লেখা থেকে জানা যায়, ১৮১৭ সালে বিক্রমপুর অঞ্চলের জীবিত এক কুলীন যার স্ত্রীর সংখ্যা শতাধিক। অপর পক্ষে তার তিন পুত্র তখন পর্যন্ত যথাক্রমে মাত্র পঞ্চাশ, পঁয়ত্রিশ ও ত্রিশটি করে বিয়ে করতে পেরেছিলেন।
৩
লেখক এই অধ্যায়ে বলেছেন হিন্দু, বিধবাদের কঠিন ব্রাহ্মচর্য বাল্যবিধবাদের জীবনে এক দুঃসহ অভিশাপ।
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বাঙালি সমাজে মেয়েদের অবস্থার আরো অবনতি হয়েছিল। একদিকে বহুবিবাহ, যার পরিণতিতে তৈরি হয় হিন্দু বিধবা সমাজ, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চাপে পড়ে অনেকে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করতো, কেউবা আত্মঘাতি আবার কারো কারো স্থান হতো কাশী অথবা বৃন্দাবনে, যেখানে পাঠিয়ে আত্মীয়স্বজন তাদের ভুলতে দেরী করতো না। যার পরিণতিতে দেবদাসী বা বেশ্যাবৃত্তি করেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করতো।
পুরো অধ্যায়টিতে বিধবাদের অমানবিক কষ্টের টুকরো চিত্র উঠে এসেছে।
লেখক আরো জানাচ্চেন, সেসময় রক্ষিতা কেবল যৌনবৈচিত্র্য বাড়ানোর পাত্রীই ছিলেন না, রক্ষক তার মধ্যে প্রেমের স্বাদ পেতেও চেষ্টা করতেন। বিবাহিত জীবনে যা পাওয়া যায়নি, সেই দুর্লভ বস্তু পাওয়ার হা-পিত্যোশ চলত পরকীয়া এবং রক্ষিতা রাখার মধ্য দিয়ে।
ঘরে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও পরনারী নিয়ে ফূর্তি করা বা রাত কাটানো স্বাভাবিক বলেই ধরে নেয়া হতো।
লেখক সেই সময়ের নাট্যজগতের বিখ্যাত অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসীর জীবন কাহিনী তুলে ধরেছেন এই অধ্যায়েই।
উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এবং ব্রাহ্ম আন্দোলনের ফলে এক নূতন পবিত্রতা ঔচিত্যবোধের দ্বারা উদ্বধিত হয়েছিলেন।
পঞ্চম অধ্যায়: পরিবর্তিত পারিবারিক মুল্যবোধ
উনিশ শতকের সূচনালগ্নে বাংলার নারীপুরুষের সম্পর্ক গর্ব করার মতো ছিল না। শিক্ষার আলোবঞ্চিত, বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্কশুন্য বাঙালি হিন্দুনারীর প্রায় সমস্ত মানবিক অধিকার থেকে ছিলেন বঞ্চিত।
নারীদের নিরুপায় অবস্থার প্রধান কারণ ছিল পরাধীনতা। ধন-সম্পদহীন নারীদের ছিল না সম্পত্তির অধিকার, ছিল না বাইরে বেরিয়ে উপার্জনের ছাড়পত্র।
মুসলমান নারীরা তুলনামূলক কিছু সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতো। তাদের সম্পত্তি অধিকার ছিল, হিন্দু বিধবাদের তুলনায় মুসলমান বিধবা-নারীদের অবস্থা ভাল ছিল; ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিধবাবিবাহের অনুমতি ছিল।
এরপরও সমাজে মধ্যবিত্ত নারীরা ছিলেন অন্তঃপুরে পর্দার আড়ালে অবগুণ্ঠনবর্তী। বহির্বিশ্ব ও অন্দরমহলের মধ্যকার দৃশ্য অথবা অদৃশ্য পাঁচিল ছিল দুর্লঙ্ঘ্য।
লেখক বিলকিস রহমান তার ‘উনিশ শতকে বাংলায় নারীপুরুষ সম্পর্ক’ বইটির শেষ অধ্যায় সূচনায় এমনটিই বলছেন।
উনিশ শতকের শেষার্ধে নারীর ‘নূতন’ ভূমিকা এবং পরিবারে নারীর কর্তব্য নিয়ে উপদেশমালা লেখা হয়।
১
উনিশ শতকে বাংলার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পুরুষরা একদিকে নারীদের শিক্ষিতা, সংস্কৃতা, সহকর্মীনী পত্নী চেয়েছিলেন যারা পাশ্চাত্যের নারীদের মতো শৃঙ্খলা মেনে কাজ করবেন, সময়ের সদ্ব্যবহার করবেন, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিশু পালন করবেন। সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভে স্বামীকে সহায়তা করবেন, অন্যদিকে প্রাচীন আর্যনারীদের দৃষ্টান্ত অনুসারে পতিসেবা করবেন, শিশুমানস গঠন করবেন এবং আপন চরিত্রমহিমায় সমগ্র পরিবার ধর্ম আলোকিত করবেন।
২
লেখকের গবেষণায় উঠে এসেছে, সমাজ সংস্কারকদের প্রচেষ্টাতেই গড়ে উঠেছিল নারীকেন্দ্রিক বিভিন্ন আন্দোলন সেই সময়েই। এইসব আন্দোলনের মধ্যে সতীদাহ বিরোধী আন্দোলন, বিধবাবিবাহ আন্দোলন, কৌলিন্যপ্রথা বিরোধী আন্দোলন, বাল্যবিবাহ, সহবাস সম্মতি ও পণপ্রথা বিরোধী আন্দোলন উল্লেখযোগ্য।
এবং শেষমেশ এসে এও জানা যায়, এত আন্দোলন, আইন প্রণয়ন, সমাজসংস্কার সবকিছুর পরেও বাল্যবিবাহ বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।
তবে এটা সত্যি যে শতকের শুরুতে সেখানে ৮ থেকে ১০ বছরের মধ্যে বিয়ে হতো শতকের শেষদিকে এসে বিয়ের ক্ষেত্রে ২-৩ বছর বাড়ে অর্থাৎ শতকের শেষদিকে মেয়েদের বিয়ে হতো সাধারণ ১২-১৪ বছর বয়সে।
৩
এখানে লেখক পণপ্রথার কথা তুলে এনেছেন, শেষদিকে বলছেন ‘যে ছেলে যত পাস, তার বাজার দর তত বেশি’। বিশেষ করে হিন্দু শাস্ত্রে যথাসাধ্য বস্ত্র-অলংকারসহ কন্যাদানের বিধান আছে।
৪
উনিশ শতকের শুরুতে সমাজে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ যে পরিমাণ শেকড়ে বিস্তৃতি লাভ করেছিল শতাব্দীর মধ্যভাগে এসব সামাজিক আচারে পরিবর্তনের ব্যাপক হাওয়া লাগে।
লেখক বলেন প্রথম দিক থেকেই সচেতন কিছু ব্যক্তি নারীশিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেন। এঁদের মধ্যে হিন্দু সমাজপতি রাধাকান্ত দেব, রামমোহন এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মতো ব্যাক্তিত্ব ছিলেন।
তবে বিশেষভাবে বাঙালি মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে এগিয়ে আসে খ্রিস্টান মিশনারিরা।
শতাব্দীর মধ্যভাগে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজপতিরা অন্তঃপুরে বসে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার মধ্যে কোনো দোষ খুঁজে পাননি। তবে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সম্পন্ন, এমনকি ‘দরিদ্র অথচ ভদ্রলোক’রাও পর্দাপ্রথা কঠোরভাবে মেনে চলতেন।
৫
এই অধ্যায়ে নারীদের নামের পাশে বাবা বা স্বামীর পদবী ব্যাবহারের নানান উদাহরণ উঠে এসেছে।
৬
এখানে লেখক তুলে ধরেছেন, নারীর অধঃস্তনতার যে অমানবিক চিত্র পরিবারে পুরুষদের চিন্তিত করে তুলেছিল, কিভাবে নিজের স্ত্রী-কন্যাকে নিরাপদে রাখা যায় তা নিয়ে যে পুরুষও উদ্বিগ্ন হয়েছিল সেই কথা।
এসেছে বিধবা হওয়ার পর রাতারাতি পুত্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় বিধবাগণ কিভাবে হয়ে উঠতেন পুত্রবধূর অবজ্ঞার পাত্র সেই চিত্র।
এসেছে উইল এ নারীর অবস্থান নিয়ে তথ্য।
৭ এবং ৮
এখানে লেখক তুলে এনেছেন অনেকগুলো কাবিননামা যার মাধ্যমে ফুটে উঠেছে নারীদের অন্যরকম একটা অবস্থা।
৯, ১০, ১১ এবং ১২
লেখক বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সচেতনতার এবং বাস্তব পদক্ষেপ হিসেবে উনিশ শতকের আর কিছু কাবিননামার উল্লেখযোগ্য অংশ তুলে এনেছেন এখানেও।
কাবিননামায় এসব শর্তের বারবার ব্যবহার থেকে মনে হয় যে, ধর্মীয় বিধিবিধানের বাইরেও বাঙালি মুসলিম সমাজে দাম্পত্যসম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু বিধিবিধান গড়ে উঠেছিল এবং তা দেশের বিভিন্ন স্থানে পালন করা হতো।
বইটির উপসংহারের একদম শুরুতেই লেখক বলেছেন, উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক বাংলায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল নারী। নারীর অধঃস্তনতার চিত্রই সে সময়ে বিদেশি লেখকদের রচনায় খুব বেশি ফুটে উঠেছে।
খুব বোবা এক কষ্টে ভুগেছি যে বিষয়টি জেনে, তা নিয়েই এই বই-লেখকের একটি অংশ দিয়ে শেষ করি। উনিশ শতকের শুরুতে অল্পবয়সী বধূমৃত্যুর হার তুলনামুলকভাবে বেশি ছিল। অল্পবয়সী নারী দাম্পত্যজীবনে প্রবেশের জন্যে পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত ছিল না, স্বামীর শারীরিক চাহিদা মেটাতে যেয়ে মৃত্যুর ঘটনা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এমন অনেক ঘটনাই অজানা আমাদের।
অল্পবয়সে নারীকে সংসারের সমস্ত কাজের চাপ সামলাতে হয়েছে বালিকা সেই বধুদের। রান্নাঘরেই যে জীবন বন্দি ছিল তা উঠে এসেছে আত্মজীবনীতে।
নারী পর্যাপ্ত আহার পেত না, ক্ষুধা লাগলেও খেতে পেত না বা কাউকে বলতেও পারতো না। ঘরের বউ সবার শেষে উচ্ছিষ্ট থাকলে খেতো, খাবার না থাকলে না খেয়ে রাত পার করতে হতো। বালিকা বধূদের অধিকাংশই অপুষ্টিতে ভুগতো।
উনিশ শতকে নারীর সূচিতা রক্ষা পরিবারের ঐতিহ্য হয়ে দারিয়েছিল। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সব ঋতুতেই, স্বামীর সঙ্গে সহবাস করুক না করুক, হিন্দু নারীকে কাকাডাকা ভোরে অন্যরা দেখার আগেই গঙ্গাস্নান করতে হতো।
বইটি লেখকের গবেষণালব্ধ, উনিশ শতকের নারী-পুরুষ সম্পর্ক বিষয়ক যেসব চিত্র উঠে এসেছে তা বড় বেশি বেদনার। এই সময়ের বাংলার নারীদের একজন হিসেবে আজকের প্ৰেক্ষিত নিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই নিজের অবস্থান নিয়েও বারবার ভেবেছি। ভাবনা এসেছে আজকের বাংলাদেশ এ নারীপুরুষ সম্পর্কের অবস্থা নিয়েও।
লেখককে সাধুবাদ দিতে হয় তার সময় এবং নিষ্ঠার জন্যে, নিঃসন্দেহে এটি আগামী যে কোন সময়ের দলিল হয়ে থাকবে।
বইটি পড়ার জন্যে পাঠক হিসেবেও আমাকে দিতে হয়েছে বেশ নিষ্ঠা এবং মনোযোগ। বইটির বিশদ আলোচনার বেশির ভাগই আমাকে ভীষণ টেনেছে পাঠক হিসাবে অন্যদের মাঝে তুলে ধরবার। সেই তাগিদ থেকেই আমার এই চেষ্টা, যারা পড়বেন তাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ দিতেই হবে লেখক এবং আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে।